এন্টিবায়েটিক র্যাজিসট্যান্স
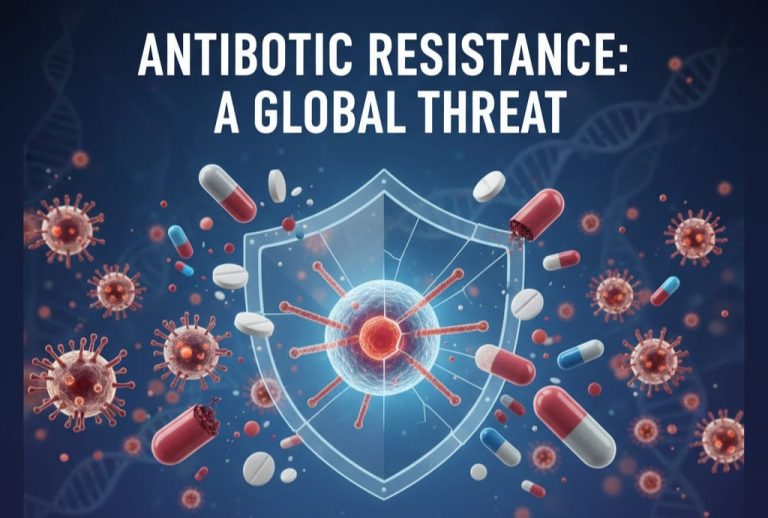
এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পর থেকে মানবজাতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিপ্লব দেখেছে। আগে যেখানে সাধারণ সংক্রমণও জীবনহানিকর হতো, সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক জীবন বাঁচিয়েছে কোটি কোটি মানুষের। কিন্তু আজ আমরা এক ভয়ঙ্কর সমস্যার মুখোমুখি — এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। অনেকেই ভুল ভাবে ধারণা করেন যে মানুষের শরীর এন্টিবায়েটিক থেকে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। আসল ঘটনা তেমন না। সত্য হলো — রেজিস্ট্যান্ট তৈরী হয় ব্যাক্টেরিয়ার শরীরে, মানুষের শরীরে নয়। সুতরাং আপনার বাচ্চার শরীরে এতগুলো এন্টিবায়েটিক রেজিস্ট্যান্ট এমনটা ভাবার কোন কারণ নাই। চলুন জেনে নেই বিস্তারিত।
এন্টিবায়োটিক কী?
এন্টিবায়োটিক হলো এমন ওষুধ যা ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এগুলো ব্যাক্টেরিয়াকে মেরে ফেলে অথবা তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। এন্টিবায়োটিক ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না। তাই ভাইরাসজনিত অসুখে এন্টিবায়োটিক খেলে কোনো উপকার নেই।
এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কী?
এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হলো এমন এক অবস্থা যখন ব্যাক্টেরিয়া নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরও বেঁচে থাকতে ও বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ—
- মানুষ নয়, ব্যাক্টেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট হয়।
- আগের যে ওষুধে একটা ব্যাক্টেরিয়া সহজেই মারা যেত, এখন সেটাতে উক্ত ব্যাক্টেরিয়া মারা যায় না।
অনেক মা–বাবা রিপোর্ট হাতে নিয়ে বলেন— “ডাক্তার সাহেব, আমার বাচ্চার শরীরের সব এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে।” আসলে এটা সঠিক নয়। আবারো বলছি রেজিস্ট্যান্ট হয় ব্যাক্টেরিয়া, মানুষের শরীর নয়। রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা বা অন্য কোনো কালচার রিপোর্টে যখন দেখা যায়—“এই জীবাণু অমুক ওষুধে সেনসিটিভ, অমুক ওষুধে রেজিস্ট্যান্ট”— তখন আসলে বোঝানো হয় জীবাণুটি ওই ওষুধে মারা যায় কি না।
একটি কালচার-সেনসিটিভিটি রিপোর্টে সাধারণত এরকম থাকে—
- জীবাণুর নাম: যেমন E. coli
- বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের তালিকা
- প্রতিটির পাশে লেখা: Sensitive (S), Intermediate (I), বা Resistant (R)
- Sensitive: ওই ওষুধে ব্যাক্টেরিয়া সহজে মারা যায়।
- Resistant: ওই ওষুধে ব্যাক্টেরিয়া টিকে থাকে।
- Intermediate: মাঝামাঝি প্রভাব।
আসলে কী হয়?
- আপনার শরীরে (বা বাচ্চার শরীরে) সংক্রমণ ঘটানো যে ব্যাক্টেরিয়া, সেটাই রেজিস্ট্যান্ট হয়েছে।
- একই শরীরে ভবিষ্যতে অন্য ব্যাক্টেরিয়া আসতে পারে, সেটি আবার একদম ভিন্নভাবে ওষুধে সংবেদনশীল হতে পারে।
- অর্থাৎ শরীর চিরতরে “সব এন্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্ট” হয়ে যায় না।
উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক
ধরা যাক, আপনার বাচ্চার রক্তে Klebsiella pneumoniae ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া গেছে। রিপোর্টে দেখা গেল—
- পেনিসিলিন → Resistant
- সেফিক্সিম → Resistant
- কার্বাপেনেম → Sensitive
এর মানে হলো এই মুহূর্তে যে জীবাণুটি রক্তে সংক্রমণ করেছে, সেটি প্রথম দুই ওষুধে টিকে যায়, কিন্তু শেষের ওষুধে মারা যায়। একজন মানুষের শরীরে এরকম রিপোর্ট পাওয়া মানে এই নয় যে সকল Klebsiella pneumoniae এই এন্টিবায়েটিক গুলোতে র্যাজিসট্যান্ট। বরং এর মাধ্যমে এটা বুঝা যায় যে Klebsiella pneumoniae প্রজাতীর ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে অনেকে নিজেকে কিছু এন্টিবায়েটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী করে গড়ে তুলেছে। অনুরুপ ভাবে আরো কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে যা এরকম নিজেদের প্রতিরোধী করে গড়ে তুলতে পেরেছে।
কেন এই বিষয়টা বোঝা জরুরি?
- অযথা আতঙ্ক এড়াতে।
- এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে ভুল ধারণা দূর করতে।
- সচেতন হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ওষুধ খাওয়ার জন্য।
- ভবিষ্যতে অকারণে এন্টিবায়োটিক না চাইতে।
ব্যাক্টেরিয়া কীভাবে এন্টিবায়েটিক এর বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স গড়ে তোলে?
- প্রাকৃতিক জেনেটিক মিউটেশন: ব্যাক্টেরিয়ার জিনে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তন যদি ওষুধের আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করে, তবে সে বেঁচে যায়।
বেঁচে থাকা ব্যাক্টেরিয়া বংশবৃদ্ধি করে এবং রেজিস্ট্যান্স বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে দেয়।
- জিন ট্রান্সফার: ব্যাক্টেরিয়া আশেপাশের অন্য ব্যাক্টেরিয়ার কাছ থেকে রেজিস্ট্যান্স জিন ধার নিতে পারে।
ব্যাক্টেরিয়ার প্রতিরোধের কৌশল
- ওষুধ ভেঙে ফেলা: ব্যাক্টেরিয়া এনজাইম তৈরি করে যা এন্টিবায়োটিককে অকেজো করে দেয়। উদাহরণ: E. coli বা Klebsiella ব্যাক্টেরিয়া β-lactamase নামক এনজাইম তৈরি করে, যা পেনিসিলিন গ্রুপের ওষুধকে অকার্যকর করে দেয়।
- ওষুধ বের করে দেওয়া: এন্টিবায়োটিক ঢুকলেও ব্যাক্টেরিয়া বিশেষ পাম্পের মাধ্যমে বাইরে ফেলে দেয়।
- ওষুধের লক্ষ্যবস্তু বদলে ফেলা: এন্টিবায়োটিক সাধারণত নির্দিষ্ট প্রোটিন বা এনজাইমে কাজ করে। ব্যাক্টেরিয়া সেটার গঠন পরিবর্তন করে, ফলে ওষুধ কাজ করতে পারে না। উদাহরণ: MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)।
- ওষুধ ঢুকতে না দেওয়া: সেল ওয়াল বা মেমব্রেন এমনভাবে বদলে ফেলে যাতে ওষুধ প্রবেশই করতে পারে না।
কেন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়?
- ভাইরাস জনিত সমস্যায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারঃ ভাইরাস মারতে এন্টিবায়োটিক কাজ করে না। কিন্তু শরীরের ভেতরে থাকা স্বাভাবিক ব্যাক্টেরিয়া অযথা ওষুধের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়।
- অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ ডোজঃ আংশিক এন্টিবায়োটিক খেলে কিছু ব্যাক্টেরিয়া মারা যায়, কিছু বেঁচে যায়। বেঁচে যাওয়া ব্যাক্টেরিয়াই রেজিস্ট্যান্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবার বাড়তে থাকে।
- বারবার ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারঃ একই এন্টিবায়োটিক ক্রমাগত বারবার অযথা খেলে ব্যাক্টেরিয়া অভ্যস্ত হয়ে যায়। জিন পরিবর্তন বা জিন ধার করে তারা ধীরে ধীরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- পশুপালনে অতিরিক্ত ব্যবহার: মুরগি, মাছ, গরু, ছাগলের খাবারে নিয়মিত এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয় রোগ প্রতিরোধের জন্য। ফলে প্রাণীর শরীরের ব্যাক্টেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে। পরবর্তীতে সেই র্যাজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে।
- হাসপাতাল-সংক্রান্ত কারণ: হাসপাতালে বিভিন্ন রোগীর মধ্যে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে।
বাস্তব উদাহরণ
- MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus): পেনিসিলিন গ্রুপের ওষুধে কাজ হয় না।
- MDR-TB (Multi Drug Resistant Tuberculosis): টিবির সাধারণ ওষুধ যেমন Isoniazid, Rifampicin কাজ করে না।
- CRE (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae): শেষ ভরসার ওষুধ Carbapenem পর্যন্ত এরা ভেঙে ফেলতে পারে।
করণীয়
- কেবলমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
- ডোজ ও সময়সীমা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- ভাইরাসজনিত অসুখে এন্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয়।
- পশুপালনে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।
- হাসপাতালগুলোতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
এন্টিবায়োটিক অবিষ্কার ও নোবেল পুরষ্কার
- আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এন্টিবায়েটিক বিষ্কারক করেন ১৯২৮ সালে।
- ১৯৪১ সালের দিকে হাওয়ার্ড ফ্লোরি, আর্নেস্ট চেইন এবং নরম্যান হিটলি এটিকে বিশুদ্ধভাবে তৈরি করে মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য করেন।
- ১৯৪৫ সালে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেইন—তিনজন একসাথে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পান।
মানব জীবনে এন্টিবায়োটিকের গুরুত্ব
- কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে: নিউমোনিয়া, সেপসিস, মেনিনজাইটিসের মতো মারাত্মক সংক্রমণে মৃত্যুর হার এন্টিবায়োটিকের আগের যুগে অনেক বেশি ছিল। এখন এসব রোগের চিকিৎসা সম্ভব।
- সার্জারি ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিরাপদ করেছে: বড় অস্ত্রোপচার, সিজারিয়ান ডেলিভারি, হৃদপিণ্ডের অপারেশন, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট—এসবই ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এন্টিবায়োটিক অপরিহার্য।
- ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব করেছে: কেমোথেরাপি নেওয়ার সময় রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এ সময় এন্টিবায়োটিক ছাড়া সংক্রমণে রোগী বাঁচানো কঠিন হতো।
- অঙ্গ প্রতিস্থাপন: লিভার, কিডনি বা হার্ট প্রতিস্থাপনের পর রোগীদের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এন্টিবায়োটিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- শিশু ও নবজাতকের জীবন রক্ষা: নবজাতকের সেপসিস, শিশুদের নিউমোনিয়া বা কান-গলা সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক না থাকলে মৃত্যুর হার অনেক বেশি হতো।
- গড় আয়ু বৃদ্ধি: সংক্রমণজনিত রোগের কারণে আগের যুগে গড় আয়ু অনেক কম ছিল। এন্টিবায়োটিকের কারণে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়েছে।
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: কেন এন্টিবায়োটিক বেশি লাগে
১. সংক্রমণ বেশি হওয়ার কারণ: বাংলাদেশ একটি নাতিশীতোষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার দেশ। এই আবহাওয়া ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। ফলে ব্যাক্টেরিয়া দ্রুত রেপ্লিকেট করে এবং দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং মানুষের ঘনবসতি। সব মিলিয়ে সংক্রমণজনিত রোগ যেমন নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ইত্যাদি বাংলাদেশে অনেক বেশি দেখা যায়।
২. এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের যৌক্তিকতা: সংক্রমণের হার বেশি হওয়ার কারণে চিকিৎসকরা তুলনামূলকভাবে বেশি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে বাধ্য হন। অনেক সময় রোগীর জীবন বাঁচাতে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণেই আমাদের দেশে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার অন্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি।
৩. অপব্যবহার রোধের প্রয়োজনীয়তা: যদিও সংক্রমণ বেশি, তাই বলে যত্রতত্র বা অকারণে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয়। ভাইরাসজনিত জ্বর বা অসুস্থতায় এন্টিবায়োটিকের কোনো দরকার নেই।
© ডাঃ আদনান আল বিরুনী
© ডাঃ আদনান আল বিরুনী
এমবিবিএস, এমএস (শিশু সার্জারী)
এসসিএইচপি (শিশু রোগ – অস্ট্রেলিয়া)
শিশু সার্জন ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
এসসিএইচপি (শিশু রোগ – অস্ট্রেলিয়া)
শিশু সার্জন ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বারঃ
আল-মারকাজুল ইসলামী হাসপাতাল
২১/১৭, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
রবি, মংগল ও বৃহ, বিকেল ৫ঃ০০ – ৭ঃ০০
সিরিয়ালের জন্য কল করুনঃ 01755515556
ইউনিএইড ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন
2-A/1, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১।
শনি, সোম ও বুধবার, সন্ধা ৭ঃ৩০ – ৯ঃ৩০
সিরিয়ালের জন্য কল করুনঃ 01333702755
Share via:
